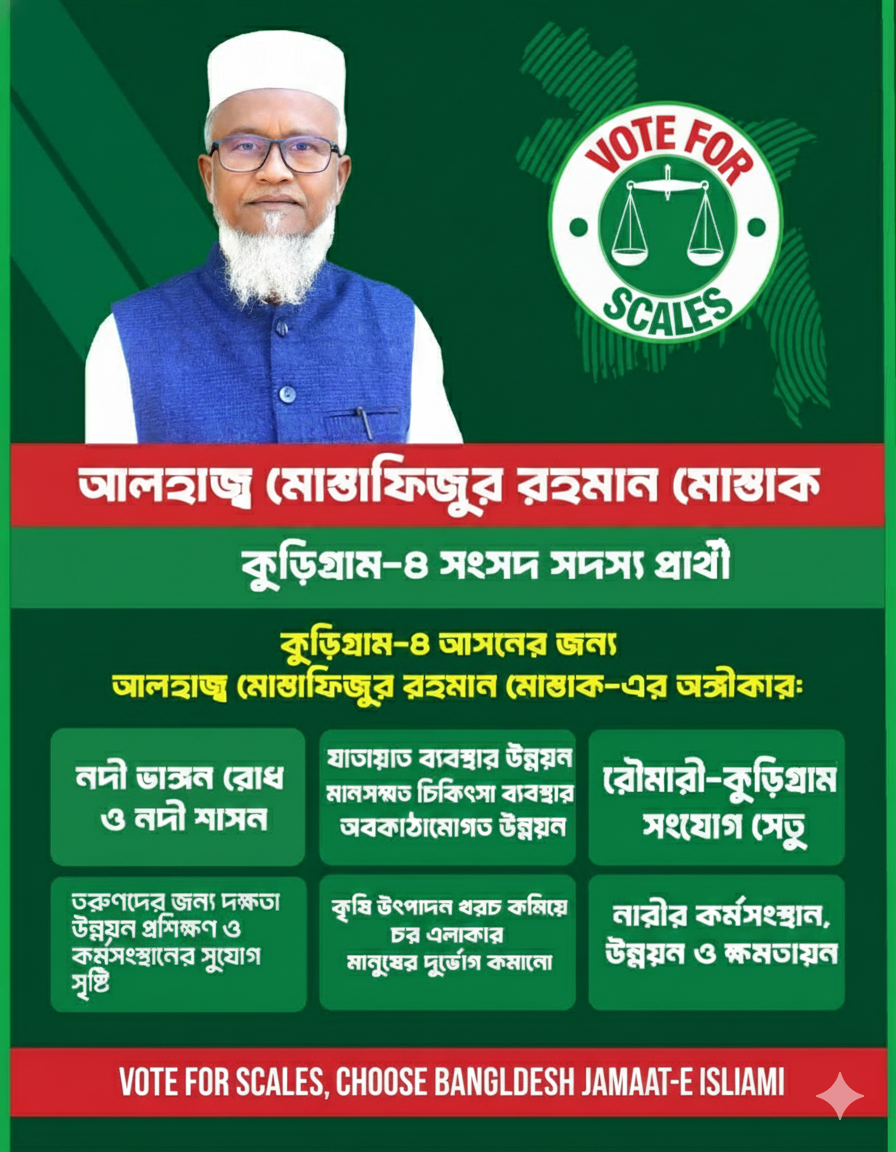নিজস্ব প্রতিবেদক:
বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা কিংবা দক্ষিণের শরীয়তপুর—যেখানেই যান না কেন, নদীর পাড় ঘেঁষে আপনি পাবেন একরাশ কান্না আর চোখে-চোখে প্রতীক্ষা। এই মানুষগুলোকে বলে “নদী ভাঙনের মানুষ”—একটি পরিচয়, যা গর্বের নয়, বেদনার, অনিশ্চয়তার।
ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, মেঘনা কিংবা পদ্মা—এই নদীগুলোর ধারে যারা বাস করে, তাদের সকাল শুরু হয় আর দশটা মানুষের মতো নয়। পাখির ডাকে নয়, ঘুম ভাঙে নদীর গর্জনে। গতকাল যে জায়গায় আবাদি জমি ছিল, আজ সেখানে নদীর স্রোত। আজ যে ঘরে রাত কেটেছে, কাল সেটি হয়তো নদীর তলদেশে। ভাঙনের এমন নিষ্ঠুর বাস্তবতায় তারা দিন গোনে, রাত কাটায়।
শুধু ঘর বা জমি নয়, নদী ভাঙন কেড়ে নেয় জীবনের স্বাভাবিকতা। হারিয়ে যায় গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাট-বাজার, শ্মশানঘাট কিংবা প্রার্থনার জায়গা। শিশুরা হারায় শিক্ষার সুযোগ, কৃষক হারায় চাষের জমি, দিনমজুর হারায় জীবিকার পথ। অনেকেই বাধ্য হয় পাড়ি জমাতে শহরের বস্তিতে, কেউ চলে যায় আত্মীয়স্বজনের কাছে, কেউ আবার রাস্তার পাশে খোলা আকাশের নিচেই গড়ে তোলে অস্থায়ী ঘর।
প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমের আগে নেতারা আসেন, প্রতিশ্রুতি দেন—“ব্যবস্থা নেওয়া হবে, বাঁধ দেওয়া হবে, পুনর্বাসন হবে।” কিন্তু এসব কথা বর্ষার পানির মতোই ভেসে যায়। একমাত্র দেখা যায় কিছু শুকনো খাবার, কিছু পুরনো কাপড় বা পলিথিনের ত্রাণসামগ্রী। তাতে বাঁচে না জীবন, মৃত্যুকে সামান্য পিছিয়ে দেওয়া যায় শুধু।
নদী ভাঙনের মানুষেরা যেন রাষ্ট্রের ‘অদৃশ্য নাগরিক’। নাগরিক সুবিধা তো দূরে থাক, অনেকের ভোটার আইডি, জন্মসনদ পর্যন্ত থাকেনা। এখানে জীবন চলে ঈশ্বরে ভরসা করে, কারণ রাষ্ট্র পাশে দাঁড়ায় না। তারা বেঁচে থাকে শুধুই টিকে থাকার জন্য, বাঁচার মতো করে বাঁচে না।
নদী ভাঙন শুধু প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়, এটি আজ একটি সামাজিক সংকট। অথচ এখনও পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে নেই কোনো স্থায়ী, টেকসই ও মানবিক পরিকল্পনা। নেই বাঁধ নির্মাণের কার্যকর ব্যবস্থা, নেই যথাযথ পুনর্বাসন বা ক্ষতিপূরণ। যা আছে, তা হলো: হাহাকার, প্রতীক্ষা আর দীর্ঘশ্বাস।
এতসব অসহায়তার মধ্যেও মানুষগুলো বাঁচে, বাঁচতে চায়। সন্তানকে স্কুলে পাঠানোর স্বপ্ন দেখে, ফসল ফলাতে চায় নতুন জায়গায়, ঘর তুলতে চায় নদীর পাড়েই আবার। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়—আর কতকাল তারা শুধু টিকে থাকবে? রাষ্ট্র কবে দেখবে তাদের? তারা কবে ‘নদী ভাঙনের মানুষ’ নয়, ‘মানুষ’ হয়ে উঠবে রাষ্ট্রের চোখে?


 Reporter Name
Reporter Name